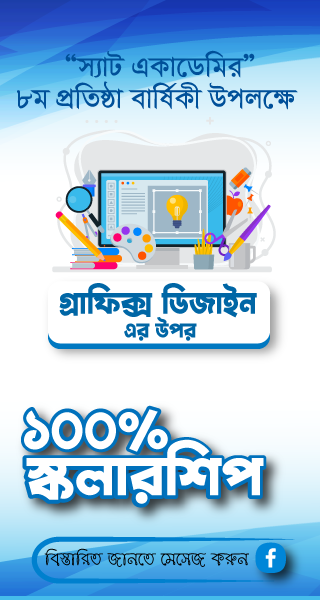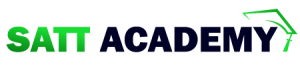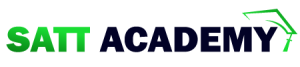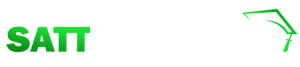৮. বানান
৮.১ বানানের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম
৮.২ কৰ্ম-অনুশীলন
৮. বানান
ভাষা শুদ্ধরূপে লিখতে হলে সে ভাষার বানান জানা খুব জরুরি। প্রত্যেক ভাষারই বানানের নিয়ম আছে। বাংলা ভাষার বানানেরও বিশেষ কিছু নিয়ম রয়েছে। এই নিয়ম সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা আধুনিক করা হয়। বাংলাদেশে সাধারণভাবে মান্য করা হয় বাংলা একাডেমি অনুমোদিত বানানরীতি। নিচে বাংলা বানানের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম দেখানো হলো।
ক. বানানে ই ঈ, উ ঊ-এর ব্যবহার
১. যেসব তৎসম শব্দের বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় স্বর ( ই ঈ, ঊ ) অভিধানসিদ্ধ, সে ক্ষেত্রে এবং অতৎসম ( তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র ) শব্দের বানানে হ্রস্বস্বর (ই,ি উ ू) হবে। যেমন :
তৎসম শব্দে :
অঙ্গুরি, অটবি, আবির, আশিস্, উষা, কিংবদন্তি, কুটির, গণ্ডি, গ্রন্থাবলি, চিৎকার, তরণি, তরি, দেশি, পদবি, বিদেশি, ভ্রু, শ্রেণি, সারণি।
অতৎসম শব্দে :
আদমি, আপিল, আমিন, আলমারি, উকিল, উর্দু, কাজি, কারবারি, কারিগরি, কুমির, কেরানি, খ্রিষ্ট, খ্রিষ্টাব্দ, গরিব, গাজি, গাড়ি, গিন্নি, চাকরি, জরুরি, জানুয়ারি, ডিগ্রি, দরকারি, দাবি, দিঘি, ধুলো, নার্সারি, পড়শি, পদবি, বাড়ি, বাঁশি, বাঙালি, বে-আইনি, ভুতুড়ে, মিস্ত্রি, মুলো, মেয়েলি, যিশু, রেশমি, লটারি, লাইব্রেরি, শাশুড়ি, শিকারি, সবজি, সরকারি, সুন্নি, হাজি, হিজরি।
২. কয়েকটি স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার হবে। যেমন :
অভিনেত্রী, কর্ত্রী, কল্যাণী, কিশোরী, গাভী, গুণবতী, চণ্ডী, চতুর্দশী, ছাত্রী, জননী, তরুণী, দাসী, দুঃখিনী, দেবী, নারী, পত্নী, পিশাচী, বিদুষী, বুদ্ধিমতী, মাতামহী, মানবী, যুবতী, লক্ষ্মী, শ্রীমতী, সতী, সরস্বতী, হরিণী, হৈমন্তী।
৩. ভাষা ও জাতির নামের শেষে ই-কার হবে। যেমন :
আফগানি, আরবি, ইংরেজি, ইরাকি, ইরানি, ইহুদি, কাশ্মিরি, জাপানি, তুর্কি, নেপালি, পাকিস্তানি, পাঞ্জাবি, ফরাসি, বাঙালি, সাঁওতালি, সিন্ধি, হিন্দি।
৪. বিশেষণবাচক ‘আলি'-প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন :
চৈতালি, পুবালি, বর্ণালি, মিতালি, মেয়েলি, রুপালি, সোনালি।
খ. বানানে ও-এর ব্যবহার
১. ক্রিয়াপদের বানানে পদান্তে ও-কার (CT) অপরিহার্য নয়। যেমন :
আনব, করত, খেলব, চলব, দেখত, ধরব, নাচব, পড়ব, বলত, মরব, মরাব, লড়ব, লিখব।
২. বর্তমান অনুজ্ঞার সামান্যরূপে পদান্তে ও-কার প্রদান করা যায়। যেমন :
আনো, করো, খেলো, চলো, দেখো, ধরো, নাচো, পড়ো, বলো, মারো, লড়ো, লেখো।
৩. ‘আনো’ প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ও-কার হবে। যেমন :
করানো, খাওয়ানো, ঠ্যাঙানো, দেখানো, নামানো, পাঠানো, শোয়ানো।
৪. অর্থ বা উচ্চারণ বিভ্রান্তির সুযোগ থাকলে কিছু বিশেষ্য, বিশেষণ ও অব্যয় শব্দে ও-কার দেওয়া আবশ্যক । যেমন :
কাল (সময়), কালো (কৃষ্ণ বর্ণ);
কোন (কী, কে, কোনটি), কোনো (বহুর মধ্যে এক) ;
ভাল (কপাল), ভালো (উত্তম)৷
গ. বানানে বিসর্গ ( ঃ )-এর ব্যবহার
১. পদান্তে বিসর্গ ( ঃ ) থাকবে না। যেমন :
ক্রমশ, দ্বিতীয়ত, প্রথমত, প্রধানত, বস্তুত, মূলত।
২. পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। যেমন :
অন্তঃস্থ, দুঃখ, দুঃসহ, নিঃশব্দ, পুনঃপুন, স্বতঃস্ফূর্ত।
৩. অভিধানসিদ্ধ হলে পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন :
দুস্থ, নিশ্বাস, নিস্পৃহ, বহিস্থ, মনস্থ।
ঘ. বানানে মূর্ধন্য-ণ ও দন্ত্য-ন-এর ব্যবহার
১. যুক্তব্যঞ্জনে (তৎসম শব্দে) ট-বর্গীয় বর্ণের (ট ঠ ড ঢ) পূর্ববর্তী দন্ত্য-ন ধ্বনি মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন : কণ্টক, ঘণ্টা, নির্ঘণ্ট, বণ্টন, অকুণ্ঠ, আকণ্ঠ, উৎকণ্ঠা, উপকণ্ঠ, কণ্ঠ, কণ্ঠনালি, লুণ্ঠন, অকালকুষ্মাণ্ড, অণ্ড, কাণ্ড, কাণ্ডারী, কুণ্ডল, খণ্ড, চণ্ডী, দণ্ড, পণ্ডিত, ভণ্ড, ভণ্ডামি৷
২. তৎসম শব্দে ঋ, ঋ-কার (, ), র, র-ফলা (, ), রেফ (´ ), ষ, ক্ষ-এর পর মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন : < ঋণ, তৃণ, অরণ্য, ত্রাণ, বর্ণ, বিদূষণ, বিশেষণ, ক্ষণ, ক্ষণিক।
৩. একই শব্দের মধ্যে ঋ, ঋ-কার, র, র-ফলা, রেফ, ষ, ক্ষ-এর যে কোনোটির পরে স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ এবং য, য়, হ, অনুস্বার (ং), – এই বর্ণগুলোর একটি বা একাধিক বর্ণ থাকলেও পরবর্তী ন-ধ্বনি মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন :
কৃপণ, নিরূপণ, অগ্রহায়ণ, অকর্মণ্য, নির্বাণ, সর্বাঙ্গীণ, অপেক্ষমাণ, বক্ষ্যমাণ৷
৪. প্র, পরা, পরি, নির- এই চারটি উপসর্গের পর নম্, নশ্, নী, নু, অনু, হন্ প্রভৃতি ধাতুর দন্ত্য-ন স্থলে মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন :
প্ৰ : প্ৰণাম, প্রণব, প্রণীত, প্ৰণিপাত,
পরা : পরায়ণ, পরাহ্ ;
পরি : পরিণতি, পরিণাম, পরিণয়,
নির : নির্ণীত, নির্ণয়, নির্ণায়ক।
৫. যুক্তব্যঞ্জন গঠনে (অতৎসম শব্দে) ট-বর্গের পূর্বে দন্ত্য-ন হয়। যেমন :
ইন্টার, উইন্টার, কারেন্ট, গ্র্যান্ড, টেন্ডার, প্যান্ট, ব্যান্ড, লন্ডন, সেন্ট্রাল৷
৬. যুক্তব্যঞ্জন গঠনে (তৎসম, অতৎসম সকল শব্দে) ত-বর্গের পূর্বে দন্ত্য-ন হয়। যেমন :
অনন্ত, অন্তরঙ্গ, একান্ত, ক্লান্ত, জ্বলন্ত, মন্ত্রী, গ্রন্থ, পান্থ, অনিন্দ্য, পরান্ন, প্রচ্ছন্ন, রান্না, সান্নিধ্য।
৭. সন্ধি ও সমাসযোগে গঠিত শব্দের বানানে দন্ত্য-ন বহাল থাকে। যেমন :
অগ্রনায়ক, অহর্নিশ, ক্ষুন্নিবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, দুর্নাম, দুর্নিবার, দুর্নীতি, নির্নিমেষ, শিক্ষাঙ্গন
৮. তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দে সর্বত্র দন্ত্য-ন হবে। যেমন :
আপন, আয়রন, কুর্নিশ, কোরান, গ্রিন, চিরুনি, ঝরনা, ধরন, বার্নিশ, মেরুন, লন্ঠন, শিহরন, হন।
ঙ. বানানে মূর্ধন্য-ষ-এর ব্যবহার
১. ঋ কিংবা ঋ-কার (.)-এর পরে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :
ঋষি, কৃষি, কৃষক, কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, তৃষিত, দৃষ্টি, সৃষ্টি, হৃষ্টচিত্ত।
২. র-ধ্বনি রেফ (′)-এর রূপ নিয়ে কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের মাথায় বসলে ঐ ব্যঞ্জনের পর মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :
আকর্ষণ, ঈর্ষা, উৎকর্ষ, বর্ষা, বর্ষণ, বিমর্ষ, মুমূর্ষু, শীর্ষ, সপ্তর্ষি, হর্ষ।
৩. অ, আ ছাড়া অন্য কোনো স্বরবর্ণ এবং ক্, র্ বর্ণের পরবর্তী দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :
ঈষৎ, ঊষা, এষণা, কোষ, জিগীষা, বিষম, ভবিষ্যৎ, রোষ, সুষমা।
৪. ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুতে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :
সঙ্গ> অনুষঙ্গ, সেক> অভিষেক, স্থান> অধিষ্ঠান, সুপ্ত> সুষুপ্ত।
৫. যুক্তব্যঞ্জন গঠনে (তৎসম শব্দে) ট-বর্গের পূর্বে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :
অনিষ্ট, অষ্টম, আড়ষ্ট, উচ্ছিষ্ট, উপদেষ্টা, কষ্ট, চেষ্টা, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠা, ভূমিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, সুষ্ঠু।
৬. যুক্তব্যঞ্জন গঠনে (তৎসম, অতৎসম সকল শব্দে) ত-বর্গের পূর্বে দন্ত্য-স হয়। যেমন :
অধস্তন, ইস্তফা, উদ্বাস্তু, ওস্তাদ, কস্তুরি, কাস্তে, জবরদস্তি, স্থান, স্থানীয়, স্বাস্থ্য।
৭. যুক্তব্যঞ্জন গঠনে (তৎসম, অতৎসম সকল শব্দে) চ-বর্গের পূর্বে তালব্য-শ হয়। যেমন :
আশ্চর্য, দুশ্চরিত্র, নিশ্চয়, পশ্চাৎ, প্রায়শ্চিত্ত, বৃশ্চিক, নিশ্ছিদ্র।
চ. বানানে রেফ (´) - এর ব্যবহার
রেফ-এর পর কোথাও ( তৎসম, অতৎসম সকল শব্দে ) ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন :
কর্জ, কর্ম, কার্য, পূর্ব, ফর্দ, মর্মর, শর্ত, সূর্য।
ছ. বানানে ঙ / ং-এর ব্যবহার
১. সন্ধিতে (তৎসম শব্দে) প্রথম পদের শেষে ম্ থাকলে ক-বর্গের পূর্বে ম্ স্থানে ং (অনুস্বার) হবে। যেমন :
অহংকার (অহম্ +কার), কিংকর, কিংবদন্তি, ঝংকার, ভয়ংকর, সংকল্প, সংকীর্ণ, সংগীত, সংঘ, সংঘাত, হুংকার।
২. উপর্যুক্ত নিয়মে সন্ধিজাত না হলে, যুক্তব্যঞ্জনে ক-বর্গের পূর্বে ম্ স্থানে ঙ (উয়োঁ)) হবে। যেমন :
আকাঙ্ক্ষা, অঙ্কুর, অঙ্গ, ইঙ্গিত, উচ্ছৃঙ্খল, কঙ্কাল, কাঙ্ক্ষিত, গঙ্গা, জঙ্গি, দাঙ্গা, পঙ্কজ, পঙ্গু, বঙ্গ, ভঙ্গি, লঙ্ঘন, শিক্ষাঙ্গন, সঙ্গী।
৩. প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে ং (অনুস্বার) ব্যবহৃত হয়।
যেমন : আড়ং, ইদানীং, এবং, ঠ্যাং, ঢং, পালং, ফড়িং, বরং, রং, শিং।
৪. তবে অনুস্বারযুক্ত শব্দে প্রত্যয়, বিভক্তি বা স্বরবর্ণ যুক্ত হলে ং স্থলে ঙ লেখা হবে। যেমন :
আড়ঙে, টঙে, ঢঙে, ফড়িঙের, রঙিন, রাঙিয়ে, সঙের।
১. আসাঢ়ে বৃষ্টি হয়। অতি বৃষ্টির পাণি পরিনামে বয়ে আনে বন্যা। লোকের কস্ট বাড়ে। দেখা দেয় বিভিন্ন রোগের প্রদুঃভাব। চলাচল দুস্কর হয়ে পড়ে।
—এই বাক্যগুলো থেকে ভুল বানানগুলো খুঁজে বের কর। সেগুলো কোন কারণে ভুল তা উল্লেখ করে শুদ্ধ বানান লেখ।
২. তোমার পাঠ্যবইয়ের যে-কোনো একটি গল্প খুব ভালো করে পড়। তারপর গল্পটি থেকে যেসব বানানে ই, উ-কার এবং যেসব স্ত্রীবাচক শব্দে ঈ-কার পাওয়া যায় সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর। (এটি তুমি একটি গ্রুপ তৈরি করেও করতে পার।)
আরও দেখুন...
Promotion